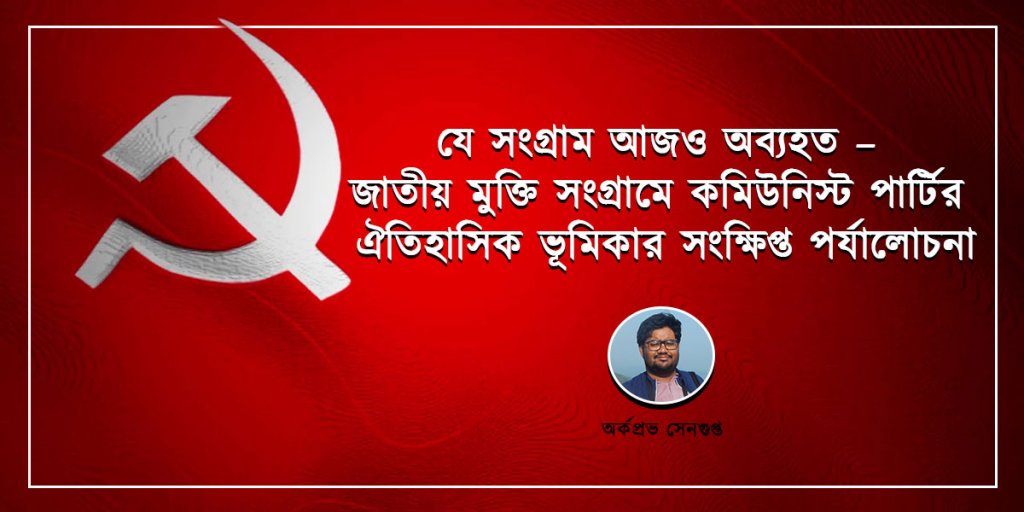
ভারতীয় জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সম্পর্কের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। রুশ বিপ্লব যখন ভবিষ্যতের গর্ভে, তখনই ১৯০৭ সালে স্টুটগার্টে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন ভিকোজী রুস্তম কামা। সেখানে র্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের মতো উপনিবেশের সমর্থক ‘সমাজতন্ত্রী’-দের আপত্তি অগ্রাহ্য করে তিনি ভারতের দুর্দশার কথা তুলে ধরেছিলেন আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রীদের মঞ্চে। বলেছিলেন – “ভারতে ব্রিটিশ শাসন চলতে থাকলে তা ভারতের বিপর্যয় ডেকে আনবে এবং ভারতীয়দের প্রকৃত স্বার্থের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হবে। এই নিপীড়িত বিশাল দেশে বসবাস করে মানবতার পাঁচভাগের একভাগ এবং তাদের বন্ধন মুক্ত করা সারা বিশ্বের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবশ্য কর্তব্য।“ এই বক্তব্য নিশর্ত সমর্থন লাভ করে লেনিন, জঁ জুর, কার্ল লিবনিখট, রোজা লুক্সেমবার্গের মতো ব্যক্তিত্বর তরফ থেকে।
কামার সঙ্গে আরেকজন ভারতীয়ও এই সম্মেলনে ছিলেন। তিনি হলেন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বীরেন্দ্রনাথের মতো সেই সময়ে ইউরোপে অনেকে ভারতীয়ই ছিলেন যাঁরা সমাজতন্ত্রে আস্থা রাখতেন, একটি স্বাধীন সাম্যবাদী ভারতের স্বপ্ন দেখতেন, কিন্তু মিটিং-সমাবেশে সহানুভূতি ও পিঠ চাপড়ানো ছাড়া তৎকালীন র্যাডিক্যাল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট – পরবর্তী কালে যাঁরা কমিউনিস্ট নামে পরিচিত হবেন, তাঁদের এই ভারতীয়দের আর কিছু দেওয়ার ছিল না। তাই তাঁদের বিদেশী সাহায্য লাভের মূল ভরসাস্থল ছিল ব্রিটেনের শত্রু দেশগুলি, এক্ষেত্রে মূলতঃ জার্মানি। এইকারণেই, আদর্শগত ভাবে কোনো মিল না থাকলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে বীরেন্দ্রনাথের মতো অনেক ভারতীয় সমাজতন্ত্রীই ইউরোপে জার্মানির সাহায্য লাভের চেষ্টা করতে থাকেন। একই কারণে ইউরোপের সক্রিয় এই বার্লিন কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আরেক মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রী স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ভুপেন্দ্রনাথ দত্তও। এঁরা তৎকালীন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদী জার্মানির সহায়তা গ্রহণ করতে বাধ্য হলেও স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে একটি সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বার্লিন কমিটি এবং প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সবাই সমাজতন্ত্রী বা সাম্যবাদী ছিলেন না, কিন্তু এই সংগঠনে সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রীদের যে গভীর প্রভাব ছিল তা অনুমান করা যায় জার্মানির সঙ্গে কমিটির চুক্তিপত্রের ১০ নং ধারা দেখে। এতে বলা হয় – “আমাদের বিপ্লব সফল হইলে ভারতে সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্র শাসন প্রবর্তন করা আমাদের অভিপ্রেত হইবে। তখন অস্ট্রো জার্মান শক্তি তাহাতে বাধা দিতে পারিবেন না।“ যাই হোক, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি পরাজিত হলে এবং ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রুশ বিপ্লবের পর এই বিপ্লবীদের প্রতি মতাদর্শিক ভাবে সহানুভূতিশীল একটি শক্তির উত্থান হলে বার্লিন কমিটির অধিকাংশ নেতৃত্বই সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্দেশ্য পাড়ি দেন। নবগঠিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নে দেশের মুক্তির আশায় প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের এই যাত্রা ব্রিটিশ সরকার ভালো চোখে দেখেনি। স্টকহোমে অবস্থিত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত এই বিষয়ে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন তার একটি লাইন দেখা যাক – “এদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে লেনিন এবং অন্যান্য ইংরেজ বিরোধী, চরমপন্থী, রুশ বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভারতের স্বাধীনতাকে জোরদার করা।“ ১৯১৯-এর মার্চ মাসে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অধিবেশনে ভারত সম্পর্কে খুবই প্রশংসাসূচক বক্তব্য রাখা হয়েছিল। বলা হয় – “ভারতে, বিপ্লবী আন্দোলনে একদিনের জন্যও ভাঁটা আসেনি। সেখানেই সংঘটিত হয়েছে এশিয়ার বৃহত্তম শ্রমিক ধর্মঘট। বোম্বাইয়ের সংগ্রামী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সাঁজোয়া গাড়ি বের করতে বাধ্য হয়েছে ব্রিটিশ শাসকরা…”। এই বক্তব্য লেনিনের ভাবনার ছায়া স্পষ্ট। কারণ সুইজারল্যান্ডে নির্বাসনে থাকাকালীনই তিনি ১৯০৮ সালের তিলকের মুক্তির দাবীতে বোম্বের শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট সমর্থন করেছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথের পাশাপাশি এই সময় মস্কোতে আগমন হয় আরেক বাঙালি বিপ্লবীর। ইনি ছিলেন বাঘা যতীনের অনুগামী, যুগান্তর দলের প্রাক্তন সদস্য নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। মানবেন্দ্রনাথ রায় নামেই তিনি তখন অধিক পরিচিত। তিনি কমিউনিস্ট রাজনীতিতে নতুন মুখ নন। মেক্সিকোর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে তাঁর ইতিমধ্যেই একটি আন্তর্জাতিক পরিচিতি ছিল। ১৯২০ সালে মানবেন্দ্রনাথ মস্কো পৌঁছন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগ দিতে।
অধিবেশনে ‘থিসিস অন ন্যাশনাল অ্যান্ড কলোনিয়াল কোয়েশ্চেন’ নিয়ে স্বয়ং লেনিনের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক হয়। দুই জনই বিষয়ে সহমত ছিলেন, ভারতে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শোষণের শৃঙ্খল মুক্ত করতে কমিউনিস্ট পার্টিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু লেনিন যেখানে মনে করেছিলেন জাতীয় সংগ্রামের এই পর্যায়ে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা কাম্য, মানবেন্দ্রনাথ রায় কংগ্রেসের রাজনীতির প্রতি প্রাক্তন বিপ্লবী সুলভ অবজ্ঞা পোষণ করতেন। তিনি শ্রমিক কৃষক রাজনীতির উপর ভিত্তি করে একক ভাবে কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি বৃদ্ধির উপর জোর দেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত লেনিনের প্রস্তাবটিই গৃহীত হয় এবং একথা অনস্বীকার্য তৎকালীন পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে এই প্রস্তাবটিই সঠিক ছিল। ১৯২০ সালের ১৭-ই অক্টোবর মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নেতৃত্বে তাসখন্দে সিপিআই-এর জন্ম হয়। যদিও এই সংগঠন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আলাদা ভাবে আবার কানপুরে প্রতিষ্ঠা করা হয়, এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এই পার্টিতে প্রথম ধাপে যে চার ধারা থেকে সদস্য এসে যোগদান করেন তাদের আলদা করে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই চারটি ধারা হল -১) বার্লিন কমিটি গোষ্ঠী – যাঁরা জার্মানি থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে এসেছিলেন ভারতের মুক্তি সংগ্রামের নতুন পথের সন্ধানে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম. বরকতুল্লা, এম.পি.বি.টি আচার্য, অবনী মুখার্জি। ২) মুহাজির গোষ্ঠী – যাঁরা খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার পর পৃথক পথের সন্ধানে ভারত ত্যাগ করেন। এঁদের অনেকেরই গন্তব্য ছিল তুরস্ক, কিন্তু তাঁরা যা চাইছিলেন তা অনেকেই তাসখন্দেই পেয়ে যান এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগদান করেন। এই গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য কয়েকজন সদস্য হলেন আবদুল মাজিদ, সৌকত উসমানী, ফিরোজুদ্দিন মনসুর। ৩) গদর গোষ্ঠী – যাঁরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে পাঞ্জাবে বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে কমিন্টার্নের সহায়তায় নতুন করে ভারতে বিপ্লবের আগুন ছড়াতে আগ্রহী ছিলেন। এঁদের ব্রিটিশ ইন্টিলেজেন্স শিখ কমিন্টার্ন এবং এর সদস্যদের গদর-বলশেভিক বলেও উল্লেখ করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রতন সিং, সন্তোষ সিং প্রমুখ। ৪) ভারত গোষ্ঠী – অহিংস অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার পর এবং বিপ্লবী রাজনীতি গুপ্তহত্যা আর স্বদেশী ডাকাতির চক্রের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে যাওয়ায় যারা পৃথক কোনো পথের সন্ধান করছিলেন এবং মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে যাঁরা সিপিআই-এর মধ্যে সেই নতুন পথের সন্ধান পান। এঁদের মধ্যে প্রাক্তন গান্ধীবাদী থেকে বিপ্লবী অনেকেই ছিলেন। এঁরাই ছিলেন সি.পি.আই-এর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী। এঁরা দেশের মধ্যেই প্রদেশে প্রদেশে কমিউনিস্ট সেল গড়ে তোলেন। এই ধারার অন্যতম উজ্জ্বল নাম হল মুজফফর আহমেদ।
কমিউনিস্টরা ভারতে নিজেদের মত ও পথের প্রচারের প্রথম সুযোগ লাভ করে ১৯২১ সালে কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে। সেখানে প্রচারিত কমিউনিস্ট ইস্তেহারে বলা হয় – ‘ভারতবর্ষকে তার মূল ভিত্তি সমেত যা কাঁপিয়ে দেয়, সেইরকম বিপ্লব যদি কংগ্রেস নেতৃত্ব দিতে চায় তবে শুধুমাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন বা উন্মাদিক সাময়িক, উদ্দীপনার উপরই যেন তাঁরা নির্ভর না করেন। ট্রেড ইউনিয়নসমূহের এই মুহূর্তের দাবিগুলিকে তাঁরা নিজেদের দাবি হিসেবে তুলে ধরুন, কিসানসভার কর্মসূচীকে তাঁদের নিজেদের কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করুন।‘ শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীকে জাতীয় সংগ্রামে যুক্ত করার এ ছিল এক অভূতপূর্ব আহ্বান। স্বামী কুমারানন্দ এবং মৌলানা হসরত মোহানি কমিউনিস্ট ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই ‘পূর্ণ স্বরাজ’-এর দাবী তোলেন এই অধিবেশনে। উল্লেখ করা যেতে পারে, এই অধিবেশনেই মৌলানা মোহানি ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ বা ‘বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক’ এই ধ্বনি তুলেছিলেন, যা পরবর্তীকালে সাম্যবাদীদের রণহুংকারে পরিণত হয় আর কুমারানন্দ বিলি করেছিলেন কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো। যাই হোক, পূর্ণ স্বরাজের এই দাবী মেনে নিতে গান্ধী সহ কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতৃত্বই রাজি ছিলেন না। একই দাবী পরের বছর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের গয়া অধিবেশনেও উত্থাপন করা হয়। এই অধিবেশনে কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে ‘ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অ্যাকশন প্রোগ্রাম’ নামে একটি ইশতেহার বিলি করা হয়েছিল কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে। এতে ব্রিটিশ সম্পত্তির জাতীয়করণের পরিবর্তে উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপকরণ, বন্টন এবং বিনিময় ব্যবস্থা (জমি, খনি, কারখানা, রেলওয়ে) অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রদান করা হয়। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দাবী ছিল পূর্বল্লেখিত পূর্ণ স্বরাজ বা স্বাধীনতার দাবী। এতকাল পর্যন্ত কংগ্রেস স্বরাজের মধ্যেই নিজেদের দাবী সীমাবদ্ধ রেখেছিল। স্বরাজ বলতে অধিকাংশ কংগ্রেস নেতাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ডোমিনিয়ন হিসেবে স্বীকৃতিকেই বুঝতেন। কিন্তু এই ইশতেহারে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে লেখা হয় – ‘জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের নেতা হিসেবে কংগ্রেসকেই সাহস করে এই পদক্ষেপ গ্রহণের স্বপক্ষে চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে এবং সন্দেহাতীত স্পষ্টতায় ঘোষণা করতে হবে যে, সর্বজনীন ভোটাধিকারের গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন এক জাতীয় সরকার গঠনের দাবী থেকে এতটুকুও কম নয় তাঁদের ঈপ্সিত লক্ষ্যবস্তু।‘ এতে এও উল্লেখ করা ছিল – ‘ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থেকে সমান অংশীদারির তত্ত্বটি সাম্রাজ্যবাদেরই একটি গিলটিকরা সংস্করণ ছাড়া কিছু নয়। এই তত্ত্বের আড়ালে যে মতলব, সেটা হচ্ছে কিছু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধাদানের মাধ্যমে দেশীয় জমিদারদের সমর্থন আদায় করা ও দেশের শোষণে তাদের ছোট শরিক হিসেবে ঠাঁই দেওয়া। এর দ্বারা আমাদের সমাজের উচ্চতর শ্রেণীভুক্তরাই কিছুটা সান্তনা খুঁজে পেতে পারে মাত্র।‘
এই সময় ভারতের কমিউনিস্টরা ধীরে কিন্তু স্থির ভাবে প্রদেশে প্রদেশে বিভিন্ন সেলে সংগঠিত হতে থাকেন। কিন্তু তাঁদের সংহত হওয়ার বিশেষ সুযোগ ব্রিটিশ সরকার প্রদান করেনি। একের পর এক মামলা সদ্যজাত কমিউনিস্ট সংগঠনের নেতা কর্মীদের কারাবন্দি করার প্রক্রিয়া শুরু হল। এর মধ্যে প্রথম উদ্যোগ ছিল ১৯২২ থেকে ১৯২৪ অবধি চারটি পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা। এতে মূলতঃ লক্ষ্য ছিল সেই সকল মুহাজির বলশেভিকরা যাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফিরছিলেন। সাত বছর অবধি কারাদন্ডে এঁরা দন্ডিত হন। ফিরোজুদ্দিন মনসুর, ইলাহী কোরবান-এর মতো পরবর্তী কালের নামকরা কমিউনিস্ট নেতারা এই মামলায় জেল খাটেন। এরপরেই শুরু হল কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা। গ্রেপ্তার হলেন এস.এ. ডাঙ্গে, মুজাফফর আহমেদ, নলিনী গুপ্ত, সৌকত উসমানী। কিন্তু মচকালেও দেশের কমিউনিস্টরা ভাঙলেন না। তাঁরা অন্য ধাতুতে গড়া ছিলেন, ব্রিটিশ শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে মেহনতি ভারতবাসীদের সাম্যের স্বদেশভূমি গড়ার যে শপথ তাঁরা নিয়েছিলেন, তা ঠুনকো ছিল না। প্রথম আন্তর্জাতিকের নির্দেশ অনুসারে তৎকালীন কমিউনিস্ট কর্মীরা এই সময় স্বরাজ পার্টি ও জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে সক্রিয় ছিলেন। একটি পৃথক কৃষক-শ্রমিক পার্টি রাজনৈতিক ফ্রন্ট হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনাও হচ্ছিল। এরই মধ্যে তাঁরা খবর পান ১৯২৫ সালে কানপুরে জনৈক সত্যভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নামে একটি দল গঠন করছে। এইরকম একটি দল আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কহীন কেউ গঠন করবে, তা স্বভাবতই সাম্যবাদীদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁরা ১৯২৫-এর ডিসেম্বরে কানপুরের সম্মেলনে যোগদান করেন। এম. সিঙ্গারাভেলু সভাপতি ও এস. ভি ঘাটে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হন এই সম্মেলনে। ১৯২৭ সালের ২৯-শে মে বোম্বেতে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সমস্ত সদস্যকে কংগ্রেসের সদস্য হওয়ার এবং কংগ্রেসের প্রতিটি শাখাতে বামপন্থী অংশ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। একইভাবে এ.আই.টি.ইউ.সি-এর মধ্যেও বাম গোষ্ঠী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়। কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে কমিউনিস্টদের অবস্থান ছিল – পূর্ণ স্বাধীনতা, স্ট্যাটুটারি কমিশন (পরবর্তীকালের সাইমন কমিশন) বর্জন, জাতীয় গণপরিষদ প্রতিষ্ঠা, সর্বজনীন ভোটাধিকার, কৃষকদের হাতে জমি, শ্রমিকদের জন্য খাদ্য ও সকলের জন্য শিক্ষা। অধিবেশনে কমিউনিস্টরা সংখ্যায় অল্প হলেও তাঁরা তাঁদের অবস্থান সোচ্চারে প্রকাশ করেন এবং বহু কংগ্রেস সদস্যকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হন। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনে কমিউনিস্টরা সোৎসাহে যোগদান করেন। ১৯২৮ সালে একের পর এক শ্রমিক আন্দোলনের ঢেউ-এ ভারত কেঁপে ওঠে। এই আন্দোলনগুলির অগ্রভাগে বহুস্থানেই ছিলেন কমিউনিস্টরা। বিশেষ করে বোম্বাই-এ সুতাকল শ্রমিকদের এই সময়ে ছয় মাস ব্যাপী ঐতিহাসিক ধর্মঘটের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই একই কালপর্বে ভারতের প্রদেশে প্রদেশে স্বাধীন কমিউনিস্ট কর্মীরা গঠন করেন নানা শ্রমিক-কৃষক পার্টি। মূলতঃ কৃষকদের মধ্যেই এই দলগুলির ভিত্তি ছিল। এর মধ্যে পাঞ্জাবে সোহন সিং যোশ-এর কীর্তি কিষাণ পার্টির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই দলগুলির সঙ্গে কমিউনিস্টদের খুবই হৃদ্যতার ও সহযোগিতার সম্পর্ক ছিল। পরবর্তী কালে যখন কেন্দ্রীয় ভাবে শ্রমিক কৃষক পার্টি গঠিত হয় এবং তার সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তার কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতিতে বহু কমিউনিস্ট স্থান পান। ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে কংগ্রেসের দুটি ধারার মধ্যে সংঘাত অব্যহত ছিল। একটি ধারা, যার মধ্যে স্বয়ং গান্ধীও ছিলেন, ছিল স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে, অপর ধারাটি পূর্ণ স্বাধীনতার অবস্থানকে সমর্থন করেছিল। কমিউনিস্টরা পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে কংগ্রেসের যে অংশটি ছিল, তাঁদেরই সমর্থন জানায় এবং এই ধারার সমর্থনেই তাঁরা পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে। ইতিমধ্যে কমিউনিস্টদের কার্যকলাপে ভীত ও শঙ্কিত ব্রিটিশ সরকার ‘নিরাপত্তা বিল’ ও ‘শিল্প বিরোধী বিল’ নামক দুটি প্রতিক্রিয়াশীল বিল কার্যকরী করার উদ্যোগ নেয়।
১৯২৯ সালে বিখ্যাত মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা কমিউনিস্টদের জাতীয় রাজনৈতিক আলোচনার একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে। এই মামলার আগে কমিউনিস্টদের নাম খুব কম লোকই জানতেন। কিন্তু মুজফফর আহমেদ, এস.এস. মির্জাকর, ধরণী গোস্বামী, এস.ভি. ঘাটে, পি.সি জোশী প্রমুখ ৩১ জন অভিযুক্তের মধ্যে ১৮ জনই আদালতকে এই মামলায় নিজেদের মতাদর্শ প্রচারের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করেন। তাঁদের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ ছিল – “…to deprive the King Emperor of the sovereignty of British India, and for such purpose to use the methods and carry out the programme and plan of campaign outlined and ordained by the Communist International.” অভিযুক্তরা দেশবাসীর পক্ষ থেকে ব্যাপক সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করেন। গান্ধীজী স্বয়ং বন্দীদের সঙ্গে দেখা করেন এবং স্বল্পকালের জন্য হলেও পণ্ডিত নেহেরু তাঁদের হয়ে ওকালতি করেন। অধিকাংশ অভিযুক্তই দীর্ঘ কারাদণ্ডে দন্ডিত হন। দমন পীড়নের ফলে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার ফলে এবং একই সঙ্গে মতাদর্শগত গোঁড়ামির কারণেও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৩০-৩৩-এর আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেনি। এই অবস্থান আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মহলে তীব্র ভাবে সমালোচিত হয়। বলা হয় জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে থেকে কার্যত কমিউনিস্টরা জাতীয় কংগ্রেসের অবস্থানকেই শক্তিশালী করে তুলছে। এ ছিল তৎকালীন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাম-বিচ্যুতির একটি নিদর্শন। তবে এটা বলা প্রয়োজন যদিও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আইন অমান্য আন্দোলন অথবা তিরিশের দশকের বিপ্লব প্রচেষ্টা – কোনোটিতেই প্রত্যক্ষ ভাবে অংশ নেয় নি। কিন্তু সাম্যবাদী মনোভাবাপন্ন এবং পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন এমন অনেকেই তিরিশের দশকের গান্ধীবাদী এবং বিপ্লবী উভয় আন্দোলনেই অবদান রেখেছেন। বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের যুব বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করা যায়। মূলতঃ আয়ারল্যান্ডের বিখ্যাত ইস্টার বিদ্রোহ (যার নেতৃত্বে ছিলেন আয়ারল্যান্ডের মার্কসবাদ ও আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামের সেতু জেমস কনোলি) থেকে প্রেরণা গ্রহণ করে মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের যুব বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়। গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, কল্পনা দত্ত, সুবোধ রায় সহ এই বিপ্লবীদের অধিকাংশই পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। উত্তর ভারতে এই সময় সক্রিয় ছিল সমাজতন্ত্রী হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের মতো সংগঠন, যার সর্বাধিক পরিচিত ও জনপ্রিয় সদস্য ছিলেন শহীদ ভগৎ সিং। এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকা বহু মানুষও পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। পরবর্তীকালে উত্তরপ্রদেশে পার্টির রাজ্য সম্পাদক কমরেড শিব ভার্মা অথবা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষ-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই সময় ভগৎ সিং স্থাপিত নওজোওয়ান ভারত সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন পরবর্তীকালের কমিউনিস্ট পার্টির আরেক সাধারাণ সম্পাদক কমরেড হরকিষণ সিং সুরজিত। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ১৬ বছর বয়সে হোশিয়ারপুরে তিনি তেরঙ্গা উত্তোলন করতে গিয়ে গুলি বিদ্ধ হন।
আদালতে সুরজিত নিজের নাম বলেছিলেন ‘লন্ডন তোড় সিং’। বাংলায় বিনয় চৌধুরী, হরেকৃষ্ণ কোঙার এবং সরোজ মুখার্জির মতো পরবর্তী কালের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা লবণ সত্যাগ্রহের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। এছাড়াও বাংলায় আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন বঙ্কিম মুখার্জি, আবদুর রেজ্জাক খান, মনি সিংহের মতো অনেকেই। বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত থাকার জন্য এই সময়েই প্রমোদ দাশগুপ্ত কারাদন্ডে দন্ডিত হন। কেরলায় লবণ সত্যাগ্রহ পরিচালনা করা সময় পি কৃষ্ণ পিল্লাই জাতীয় পতাকাকে রক্ষা করতে পুলিশের সঙ্গে কালিকট সমুদ্র সৈকতে প্রত্যক্ষ সংঘাতের নেতৃত্ব প্রদান করেন। এই একই সময়ে সত্যাগ্রহে সক্রিয় ছিলেন এ.কে.গোপালনও। আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য কারাবাস করতে হয় ই.এম.এস নাম্বুদিরিপাদকেও। অন্ধ্রে একই ভাবে আইন অমান্য আন্দোলন ও কারাবাসের মধ্যে দিয়েই রাজনৈতিক পরিপক্কতা লাভ করেন পি. সুন্দরাইয়া, পি. মল্লিকার্জুন রাও-এর মতো নেতারা। কমিউনিস্ট পার্টি দল হিসেবে তৎকালীন আইন অমান্য আন্দোলনে তেমন ছাপ না রাখলেও, উপরোক্ত উদাহরণ থেকেই স্পষ্ট, যাঁরা পরবর্তী কালে কমিউনিস্ট পার্টির দায়িত্ব হাতে নিয়েছিলেন, পার্টিকে গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা অধিকাংশই আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রশ্ন হল এঁরা পূর্ব রাজনীতি ত্যাগ করে কমিউনিস্ট আন্দোলনে এলেন কেন ? তার কারণ হল কারাবাসে বিপ্লবীরা ক্রমে উপলব্ধি করেন তাঁরা যে পথে এতদিন চলছিলেন সেই পথে ভারতের মুক্তি সম্ভব নয়, কারাগারেই কমিউনিস্ট আদর্শের সংস্পর্শে এসে তাঁরা এই পথকেই ভারতের মুক্তির পথ বলে গ্রহণ করেন। একই সঙ্গে গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর গান্ধীবাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ বহু কংগ্রেস কর্মীও নতুন পথের সন্ধান করছিলেন যার মাধ্যমে দেশকে মুক্ত করা সম্ভব হবে। তিরিশের দশকের শেষভাগে এই দুটি ধারাই যে কমিউনিস্ট পার্টিতে এসে মিললেন, এ কোনোভাবেই কাকতালীয় নয়। জাতীয় মুক্তির পন্থা হিসেবে কমিউনিস্ট রাজনীতিকে এই দুই গোষ্ঠীই সচেতন ভাবে বেছে নিয়েছিলেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কমিনটার্নের সপ্তম কংগ্রেসে জর্জি ডিমিট্রভের যুক্তফ্রন্ট নীতি গৃহীত হয়। এর ভিত্তিতে ভারতীয় কমিউনিস্টরা তাঁদের পূর্বতন বাম সংকীর্ণতাবাদের নীতি পরিত্যাগ করেন। জর্জি ডিমিট্রভ-এর এই বিষয়ে অবস্থান ছিল সুস্পষ্ট। তাঁর পরামর্শ ছিল ভারতের জাতীয় পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কমিউনিস্টদের উচিৎ সরাসরি জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে প্রবেশ করে তাঁদের কাজকর্ম পরিচালনা করা। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে তাঁরা দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের অগ্রভাগে আসতে পারবেন এবং কংগ্রেসের মধ্যে বিপ্লবী বামপন্থী অংশটিকে সংহত করাও তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে। এই প্রস্তাবের পরিপূরক হিসেবে ভারতের কমিউনিস্টদের রূপরেখা হিসেবে রজনী পাম দত্ত ও বেন ব্র্যাডলে রচনা করেন দত্ত-ব্র্যাডলে থিসিস। এই থিসিসেও বাম-সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করে একটি বৃহত্তর অ্যান্টি-ইম্পেরিয়ালিস্ট পিপলস ফ্রন্ট গঠনের কথা বলা বলা হয়। নতুন এই নীতি নিয়ে প্রাথমিক ভাবে সংশয় থাকলেও, কমিউনিস্টরা অচিরেই যুক্তফ্রন্ট নীতি মেনে কংগ্রেসের মধ্যে দলে দলে প্রবেশ করতে থাকেন। এর ফলে কংগ্রেসের মধ্যে লেফট ব্লকের শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৬ সালে লখনউ কংগেসে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে কংগ্রেস সভাপতি করা হয়েছিল এই ক্রমবর্ধমান বামপন্থী ব্লককে তুষ্ট করতেই, অন্ততঃ ই.এম.এস এইরকমই মনে করেছিলেন।
এই অধিবেশনে কংগ্রেসের ম্যানিফেস্টোতেও সাম্যবাদীদের প্রভাব ছিল স্পষ্ট। অর্থনৈতিক বৈষম্য ও দারিদ্র্যর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, অঙ্গীকার করা হয় কৃষি ব্যবস্থার রূপান্তরের, শিল্প শ্রমিকদের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের, লিঙ্গ বৈষম্যের অবসানের। কংগ্রেসের মঞ্চে এই সকল বিষয় আগে এত গভীর ভাবে উত্থাপিত বা আলোচিতই হয়নি, রাজনৈতিক কর্মসূচী ও ইশতেহার-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া তো অনেক পরের কথা। এ.আই.সি.সি-এর ‘রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংবাদ বিভাগ’-এর দায়িত্ব এই সময় পেয়েছিলেন জেড.এ. আহমেদ এবং কে.এম আস্রফ। এছাড়াও হীরেন মুখার্জি, মুজাফফর আহমেদ সহ অনেক কমিউনিস্ট নেতাই এই সময় এ.আই.সি.সি-এর সদস্য হন। তবে এও ঠিক, এই ছোটো ছোটো বিজয়গুলি ছাড়াও কমিউনিস্টরা নেহেরুর কাছে আরও অনেক কিছু আশা করেছিলেন। পরিতাপের বিষয়, নেহেরু কমিউনিস্টদের এবং সেই সময়ে কমিউনিস্টদের কংগ্রেসের অভ্যন্তরে লেফট ব্লকের অন্যতম সঙ্গী জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বাধীন সোশ্যালিস্টদেরও খুবই হতাশ করেছিলেন। কারণ তিনি যে যে কথা বিভিন্ন ভাষণে বলতেন, যার সঙ্গে লেফট ব্লক সহমত ছিল, তা অধিকাংশই গান্ধীজী নাকচ করে দিতেন এবং কংগ্রেসে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হত, প্রায় সবই ছিল নেহেরুর অবস্থানের পরিপন্থী। পন্ডিত নেহেরুর মৌখিক প্রতিবাদের অধিক এই বিষয়ে কিছু করা সম্ভব ছিল না। এই কারণে আপাত দৃষ্টিতে ১৯৩৭ সালে ফৈজপুর কংগ্রেসে নেহেরুর সভাপতি পদে পুনরায় নির্বাচন বামদের বিজয় হিসেবে মনে হলেও আদতে এ ছিল কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশেরই বিজয়। তাঁরা এমন একজন সভাপতি খুঁজছিলেন যিনি মুখে বামপন্থী হলেও কার্যত মহাত্মা গান্ধীর এবং কংগ্রেস দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে গুরুতর বিবাদে যাবেন না। জওহরলাল ছিলেন তেমনই সভাপতি। এই প্রেক্ষিতে হরিপুরা কংগ্রেসের সময় কমিউনিস্টরা তাঁদের সমস্ত শক্তি দিয়ে সুভাষচন্দ্র বসুকে সমর্থন করেন। সুভাষ কমিউনিস্ট ছিলেন না, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর তাত্ত্বিক ধারণা জওহরলালের মতো পরিষ্কার ছিল না। কিন্তু তিনি নিঃসন্দেহে অনেক নির্ভরযোগ্য মিত্র ছিলেন। কমিউনিস্টরা চমৎকৃত হয়ে দেখেছিলেন হরিপুরায় ভাষণে সুভাষচন্দ্র সুস্পষ্ট একটি সমাজতান্ত্রিক রূপরেখা প্রদান করলেন। সেই রাষ্ট্র হবে পরিকল্পিত অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে পরিচালিত, ভূমি সংস্কার, জমিদারী প্রথা বিলোপ, সমবায় প্রথার বিস্তার, কৃষি ঋণ মকুব, শিল্পের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি এমন অনেকগুলি প্রস্তাব তিনি বক্তৃতায় রাখেন যা কমিউনিস্টদের কর্মসূচীর সঙ্গে অভিন্ন ছিল। সুভাষচন্দ্রকে ঘিরে কমিউনিস্টদের মধ্যে এমন উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল, যা আগে কখনও দেখা যায় নি, বিশেষ করে বাংলার কমিউনিস্টদের আলাদা আবেগ ছিল। স্বয়ং মুজফফর আহমেদ জীবনে প্রথমবার খাদি পরিধান করে হরিপুরায় গিয়েছিলেন। সুভাষ যেভাবে জওহরলাল নেহেরুর মতো দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্বের নিকট নতি স্বীকার করেনি, তার ভিত্তিতে কমিউনিস্টরা তাঁকেই কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বাম ব্লকের সঠিক নেতা বলে স্বীকার করে নেন। এই ভিত্তি ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরী অধিবেশনে গান্ধীজির মনোনিত প্রার্থী পট্টভি সিতারামাইয়ার বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করে কমিউনিস্টরা আদতে জাতীয় কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের মৌরসিপাট্টাকেই চ্যালেঞ্জ জানান। সুভাষের বিজয়ের জন্য কমিউনিস্টরা আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেন। হীরেন মুখার্জির মতে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ন্যাশনাল ফ্রন্টই সর্বপ্রথম সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতি পদে পুনঃনির্বাচনের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছিল।
সুভাষচন্দ্রের সমর্থনে পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পি.সি. জোশী যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তা এই ক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে – “ভারতীয় কমিউনিস্টরাই প্রথম রাষ্ট্রপতি বসুর পুনঃনির্বাচনের দাবী জানিয়ে ঘোষণা করেন রাষ্ট্রপতি বসু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন বলিয়া আমরা আনন্দিত…আমাদের জনগণ আন্দোলন করিতেছে। আমরা যদি আন্দোলনের ঐক্য বজায় রাখতে পারি এবং সংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারি, আমাদের জয় সুনিশ্চিত। রাষ্ট্রপতি বসু কংগ্রেসের ঐক্য রক্ষা করিতে পারিবেন।…ত্রিপুরীতে আমরা যুদ্ধ যাত্রার আদেশ পাইব এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রামের সুস্পষ্ট নির্দেশও পাইব।“ ত্রিপুরীতে স্বয়ং গান্ধীজীর প্রভাবকে তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করেও কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশ বিজয় লাভ করতে অক্ষম হয়। সুভাষচন্দ্র স্বল্প ভোটে হলেও পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করে পুনরায় কংগ্রেসের সভাপতি (রাষ্ট্রপতি) নিযুক্ত হন। এই পর্যায়ে সুভাষের সঙ্গে প্যাটেল-রাজাগোপালাচারী-গোবিন্দবল্লভ পন্থের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী ব্লকের যে সংঘাত লক্ষ্য করা যায় তাতেও কমিউনিস্টরা সুভাষের পক্ষ নেন। ‘পন্থ প্রস্তাব’-এর বিরুদ্ধে তাঁরাই সংশোধনী এনে পাল্টা ‘ন্যাশনাল ডিমান্ডস’ উত্থাপন করেন। এতে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলির সঙ্গে কংগ্রেসের সংযুক্ত ফ্রন্ট গড়ে তোলা এবং শ্রমিক-কৃষকদের অর্থনৈতিক আন্দোলনগুলিতে কংগ্রেসের সক্রিয় সমর্থন। বলা বাহুল্য, শ্রেণী সংগ্রাম থেকে শত হস্ত দূরত্ব রাখা, জমিদার ও শিল্পপতিদের অর্থে পুষ্ট কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশের কাছে এই প্রস্তাব ছিল গরম লৌহের ছেঁকার মতো। বলাই বাহুল্য এই প্রস্তাবের অধিকাংশই গৃহীত হয় নি। কিন্তু কংগ্রেসী দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের একটি বিকল্প কর্মসূচীর সন্ধান এতে ছিল। পরবর্তী কালে ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করার সময় সুভাষ নতুন দলের যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন, তা ছিল কার্যত এই প্ল্যান অফ অ্যাকশনেরই প্রতিলিপি। হরিপুরায় শেষ পর্যন্ত সুভাষ রাজনৈতিক ভাবে পরাজিত হলেও কমিউনিস্টদের তাঁকে সমর্থনের কথা তিনি ভোলেননি। তাঁর উক্তি ছিল – “আমি সর্বদাই মনে করে এসেছি এবং বিশ্বাস করি যে মার্কস এবং লেনিন অনুসারী কমিউনিজম এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের আদর্শ ও নীতিসমূহ সর্বদাই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামগুলির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাঁদের বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রাম ওতপ্রোতভাবে জোড়িত।“ চল্লিশের দশকে আদর্শগত বিরোধের কারণে সভাষপন্থীদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের বিরোধ ও তিক্ততা এই সহযোগিতার ইতিহাসকে মুছে দিতে পারে না। ১৯৩৬ সাল থেকে প্রথমে জওহরলাল নেহেরু এবং পরে সুভাষচন্দ্র বসুকে সামনে রেখে নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা কংগ্রেসের মধ্যেই সক্রিয় থেকে তার বামপন্থী অংশকে শক্তিশালী করতে প্রয়াসী হন এবং কংগ্রেসকে একটি বৈপ্লবিক সংগঠনে পরিণত করার চেষ্টা করেন। হরিপুরায় সুভাষের স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী মনোনিত প্রার্থীর বিপক্ষে জয়কে কমিউনিস্টরা নিজেদের জয় বলেই মনে করেছিলেন। কিন্তু অচিরেই স্পষ্ট হল এই জয়ের মধ্যে রয়েছে নির্মম হার। সুভাষ জিতলেন বটে, কিন্তু গান্ধীজীর সম্পূর্ণ অসহযোগিতার মধ্যে তাঁর পক্ষে কংগ্রেস পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। তাই শেষ পর্যন্ত তাঁকেই সরে আসতে হল।
কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কংগ্রেসকে বিপ্লবী সংগঠনে পরিণত করার কমিউনিস্টের প্রচেষ্টায় এইখানেই ইতি ঘটল। তবে একথা অনস্বীকার্য এই সময়ে একের পর এক শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে তাঁরা ক্রমশ তাঁদের প্রভাব বৃদ্ধি করছিলেন এবং এই আন্দোলনগুলিকে বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সর্ব ভারতীয় কৃষক সভার শক্তি এই সময়েই দ্রুত বেগে বাড়তে থাকে। এতদিন অবধি অবহেলিত শ্রমিক ও কৃষকদের দাবীগুলিকে তাঁরা কংগ্রাসের সর্বোচ্চ মঞ্চে তুলে ধরতেও সক্ষম হন। জয় হিসেবে এগুলি নেহাত তুচ্ছ করার মতো ছিল না। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনকে ঠিক যে আপোষহীন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়মুক্তি সংগ্রামের দিকে কমিউনিস্টরা পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন, তা করতে তাঁরা অক্ষম হন। ইতিমধ্যে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হলে কমিউনিস্টরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে এই যুদ্ধকে চিহ্নিত করেন। ২-রা অক্টোবর বোম্বাইতে প্রায় ৯০ হাজার শ্রমিকের একটি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়, তাতে ঘোষণা করা হয় – ‘মানবতার বিরুদ্ধে এই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে পরাজিত করাই হবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শ্রমিক ও জনসাধারণের কর্তব্য।‘ ব্রিটিশ বিরোধী শ্রমিক আন্দোলন কমিউনিস্ট প্রভাবে ক্রমশ জঙ্গী রূপ ধারণ করতে থাকে। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে প্রায় ১ লক্ষ ৭ হাজার সুতাকল শ্রমিক কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে ধর্মঘটে শামিল হন। কৃষক আন্দোলনও পিছিয়ে ছিল না। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে পালসায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত কৃষক সভার অধিবেশনের প্রস্তাবে বলা হয় – ‘এই সভা আরও বিশ্বাস করে যে, একটি বিদেশী সরকারের কর্তৃত্বকে অমান্য করতে এবং দেশের সমগ্র সম্পদ বিদেশে চালান দেবার প্রতিরোধে, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের পুরোভাগে থাকবার জন্য বরাবরের মতো জীবনের সর্বোচ্চ ঝুঁকি নিয়েও কৃষকরা নিজেরাই শ্রমিকদের সঙ্গে এসে দাঁড়াবেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে নিজেদের সভার নেতৃত্বে দৈনন্দিন সংগ্রাম শুরু করতে কৃষকদের অবিলম্বে উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিৎ। এই সংগ্রামগুলিই তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়ে এবং ব্যপক এলাকা জুড়ে সম্প্রসারিত হয়ে সত্বর এক দেশব্যাপী কর-বন্ধ খাজনা-বন্ধ অভিযানে পরিণত হবে। এবং সেই অভিযানই সাম্রাজ্যবাদীদের এই পরোপজীবী অর্থনৈতিক শক্তির অবসান ঘটাবে এবং এদেশে ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতার আসনকে টলিয়ে দেবে।‘ শ্রমিক ও কৃষকদের নিয়ে কমিউনিস্টদের এই ব্রিটিশ বিরোধী তৎপরতাকে গোড়াতেই ধ্বংস করে দেওয়ার প্রচেষ্টা করল ব্রিটিশ সরকার। পার্টির মুখপত্র ‘ন্যাশনাল ফ্রন্ট’ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। প্রায় পাঁচ শত কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীকে রাতারাতি বিনা বিচারে গ্রেপ্তার করা হল। প্রায় দুই বছর ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর পর, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে নাৎসি জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করলে কমিউনিস্টরা সিদ্ধান নেন যুদ্ধের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। এতকাল এই যুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে সংঘাত, এই সংগ্রামে ভারতের মেহনতি মানুষের কোনো স্বার্থ জড়িত ছিল না। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের যদি নাৎসি আক্রমণে পতন হয়, তাহলে ভারতে তাঁরা যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবের প্রচেষ্টা করছেন, তা কখনই সফল হবে না। এই প্রেক্ষিতে তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নেন, যে এই যুদ্ধ এখন ‘জনযুদ্ধ’-এ রূপান্তরিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিস্ট শক্তির পরাজয়ই এখন মূল লক্ষ্য। এই কারণে তাঁরা যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব ত্যাগ করেন। আচমকা এই অবস্থান পরিবর্তনের ফলে এবং ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করার জন্য মধ্য তিরিশের দশক থেকে জাতীয় আন্দোলনে এবং কংগ্রেসের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির যেটুকু প্রভাব গড়ে উঠেছিল তার অনেকটাই ধুয়ে মুছে যায়। পরবর্তী কালে স্বয়ং স্তালিন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির এই অবস্থান ও সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু এইটাও এর পাশাপাশি বলা প্রয়োজন এই সিদ্ধান্তের পেছনে কোনো ক্ষমতালোভী সুবিধাবাদী মানসিকতা কাজ করেনি, কিছুটা বাস্তব রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বিহীন হলেও যা কাজ করেছিল, তা হল বিশুদ্ধ আদর্শবোধ। ঠিক এই সময়েই বাংলার দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষিতে কমিউনিস্টরা জোর কদমে বাংলায় রিলিফের কাজ শুরু করে, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মতো সংগঠন করে গড়ে তোলে, ফ্যাসিবিরোধী শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চাকে এক নতুন মাত্রা দান করে। এইগুলি কম গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল না। ঠিক এই একই সময়ে ক্রমবর্ধমান মুসলিম লীগের প্রভাব বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টির একাংশ এমন একটি সিদ্ধান্ত নেয়, যা তাঁদের কংগ্রেসী আক্রমণের জন্য আরও উন্মুক্ত করে দেয় ও যার জন্য তাঁদের দীর্ঘকাল রাজনৈতিক মূল্যও দিতে হয়েছিল। বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ড. গঙ্গাধর অধিকারীর অধিকারী থিসিস। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর ‘ফর্মুলা’-এর অনুকরণে এবং সোভিয়েত যুক্তরাজ্য ব্যবস্থার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে গঙ্গাধর অধিকারী প্রস্তাব দেন পাকিস্তানের দাবী মেনে নেওয়া হোক যতক্ষণ তা ভারত ইউনিয়নের মধ্যেই মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বশাসনের দাবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে, ঠিক যেমন সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলি আলাদা প্রজাতন্ত্র হয়েও সামগ্রিক ইউনিয়নের অংশ। সমগ্র থিসিসটি রাজাজী ফর্মুলার থেকে খুব পৃথক ছিল না। অধিকারীর উদ্দেশ্যও অসাধু ছিল না। কিন্তু বিষয়টি ঘিরে এমন বিতর্ক সৃষ্টি হয়, যার জন্য আজও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয় তাঁরা পাকিস্তান সমর্থন করেছিলেন। অধিকারী থিসিস প্রকাশিত হওয়ার পরেও তা রজনী পাম দত্ত, বি.টি. রণদিভে, ভবানী সেনের মতো নেতাদের সমর্থন লাভ করেনি। ১৯৪৬ সালে অধিকারী নিজেই এই থিসিস ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করেন। রণদিভের এই বিষয়ে বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন – ‘আমাদের দেশের জনগণ সবসময়েই ভারতকে এক এবং অবিভাজ্য বলে মনে করতেন এবং তাঁদের কাছে আত্মনিয়ন্ত্রণ বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ধারণাটি দৈব অভিশাপের মতই অবাঞ্ছিত ছিল।…এই পরিস্থিতিতে কমিউনিস্টদের বক্তব্য সম্পর্কে ব্যপক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল এবং তার ফলে তারা জনসাধারণ থেকে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।‘ জনযুদ্ধের নীতি, আগস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করা ও অধিকারী থিসিসের ভুল বুঝাবুঝির ধাক্কা সামলে, তিরিশের দশক থেকে সঞ্চিত রাজনৈতিক পুঁজির অনেকটাই হারিয়ে গেলেও ১৯৪৬ সালে কমিউনিস্টরা আবার স্বমহিমায় ফিরে আসেন। এই সময় তাঁরা ক্রমবর্ধমান গণক্ষোভকে সঙ্গী করে এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হন, যাঁকে অনেকেই বলেছেন ‘প্রায় বিপ্লব’। আই.এন.এ-এর অফিসারদের বিচার শুরু হলে সারা দেশব্যাপী যে আন্দোলন শুরু হয় তার অগ্রভাগে ছিলেন কমিউনিস্টরা। রশিদ আলি দিবসে পুলিশের সঙ্গে কলকাতায় যে দফায় দফায় সংঘাত হয়, তাতেও কমিউনিস্টরা ছিলেন সবার আগে। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নৌ-বিদ্রোহ শুরু হয় বোম্বাই-তে। বিদ্রোহী নাবিকরা কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা জাহাজে তুলে দেয়। কিন্তু এই তিন দলের মধ্যে একমাত্র কমিউনিস্টরাই বিদ্রোহ সমর্থন করেছিলেন নিশর্ত ভাবে। বিদ্রোহীদের সমর্থনে বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত হয় শ্রমিক ধর্মঘট। রাস্তায় রাস্তায় লাল ঝান্ডাধারী শ্রমিকের সঙ্গে সেনার সংঘর্ষ হয়। কমিউনিস্ট নেতা কৃষ্ণ দেশাই সেনার মেশিনগান সেনাবাহিনীর দিকেই ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, এমন ছিল শ্রমিকদের জঙ্গি মানসিকতা। তিন দিন ধরে বোম্বাইয়ের রাস্তায় এই আন্দোলন নতুন ইতিহাস রচনা করে। এই একই বছরে বাংলায় তেভাগা আন্দোলন গতি লাভ করে, কেরলায় পুন্নাপ্রা-ভায়লারের গণসংগ্রাম সংঘটিত হয়, তেলেঙ্গানায় কৃষক বিদ্রোহ আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে। যখন সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে উঠে গণ-আন্দোলনের আগ্নিশিখায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চিরতরের মতো দেশ থেকে বহিষ্কারের সম্ভবনা দেখা দিয়েছে, ঠিক সেই সময়েই সাম্প্রদায়িক সংঘাত দেখা দিল জনগণের ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে দিল। মুসলিম লীগ তো এই ক্ষেত্রে চুড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক ভূমিকা পালন করেইছিল, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসেরও এই পরিস্থিতির জন্য যথেষ্ট দায়িত্ব ছিল। জনগণ গণ আন্দোলনের জন্য তৈরি ছিল। এই গণ আন্দোলন সাম্প্রদায়িক দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষমও ছিল। কমিউনিস্টরা নিজেরা তা করে দেখিয়েছিলেন। কংগ্রেস যদি তার বিপুল ক্ষমতা নিয়ে গণ আন্দোলনে নামত, তাঁরাও দেশের সাম্প্রদায়িক বিভাজন আরও ভালভাবে রুখতে পারতেন। কিন্তু ক্ষমতার মুখোমুখি এসে তাঁদের তখন গণআন্দোলনে যাওয়ার ধৈর্য ছিল না। লীগের সঙ্গে এইপ্রকার বোঝাপড়া করে ক্ষমতা বাঁটোয়ারা করে নিতে পারলেই তাঁরা খুশি ছিলেন। কার্যত হলও তাই। ১৫-ই আগস্ট, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাজিত হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের অশ্রুর মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা এলো। বলা হয় কমিউনিস্টরা নাকি স্বাধীনতা বিরোধী, তার সর্বাপেক্ষা বড়ো প্রমাণ তাঁদের স্বাধীনতার পরে দেওয়া স্লোগান, ‘ইয়ে আজাদি ঝুটা হে!’। কি বেদনা, কি নিদারুণ যন্ত্রণা এই স্লোগানের জন্ম দিয়েছিল, যাঁদের দেশাত্মবোধ ১৫-ই আগস্ট পতাকা নাড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাঁদের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যখন থেকে তাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তখন থেকে কমিউনিস্টরা চেয়েছিলেন ব্রিটিশ শাসনের অবসানে এক সমাজতান্ত্রিক ভারত তাঁরা দেখবেন যা হবে মেহনতি মানুষের। তার বদলে স্বাধীনতা এলো দেশের মানুষের মূলগত অবস্থার কোনো বদল না ঘটিয়ে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করে নয়, তার সঙ্গে রফা করে, মেহনতি মানুষের ভ্রাতৃত্বের উপর ভিত্তি করে নয় সাম্প্রদায়িক বিভাজনের মধ্যে দিয়ে। এই ক্ষোভ, এই স্বপ্ন ভঙ্গের যন্ত্রণা থেকেই ‘ইয়ে আজাদি ঝুটা হে, লাখো ইনসান ভুখা হে !’ এই স্লোগান তাঁরা দিয়েছিলেন। বাম হঠকারিতার একপ্রকার নিদর্শন হলেও অন্ততঃ আংশিক ভাবে এই স্লোগান সঠিক। আজাদ হিন্দ বাহিনীর ঝাঁসির রানী ব্রিগেডের ক্যাপ্টেন ও পরবর্তী কালের সিপিআই(এম) নেত্রী লক্ষী স্বামীনাথন বলেছিলেন – ‘স্বাধীনতা তিন প্রকার। একটি হল শাসকের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা, দ্বিতীয় হয় অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাধীনতা এবং তৃতীয়টি হল সামাজিক স্বাধীনতা। ভারত এর মধ্যে একমাত্র প্রথমটিই অর্জন করেছে।‘ কমিউনিস্টরা চিরকালই মনে করে এসেছে দেশ মানে দেশের সরকার নয়, দেশ সিংহবাহিনী ভারত মাতা নয়, দেশ দেশের মাটি নয়, দেশ এমনকি সীমান্ত ঘেরা মানচিত্রও নয়। দেশ হল দেশের মানুষ। তাই যতদিন পর্যন্ত দেশের মানুষ রাজনৈতিক স্বাধীনতার সাথে সাথে অর্থনৈতিক আর সামাজিক স্বাধীনতা পাচ্ছে ততক্ষণ স্বাধীনতা সম্পূর্ণ নয়। তাঁরা মনে করেন শত শহীদের রক্তে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি সার্থক করা কমিউনিস্টদের দায়িত্ব। কারণ এই স্বাধীনতা ”ঝুটা” না হলেও অবশ্যই ”অধুরা”। এই দিক থেকে ‘সম্পূর্ণ স্বরাজ’-কে সামনে রেখে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি স্বদেশকে মুক্ত করার যে প্রচেষ্টা বিংশ শতকের কুড়ির দশকে শুরু করেছিল, স্বাধীনতা উত্তর ভারতে তাঁদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড সেই প্রচেষ্টারই যৌক্তিক পরিণতি। অন্য রাজনৈতিক দলের স্বাধীনতা দিবস পালনের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীনতা দিবস পালনের এটিই মূল পার্থক্য। তাঁদের কাছে ১৫-ই আগস্ট শুধু অতীত সংগ্রামের স্মৃতিচারণার দিন না, একই সঙ্গে অসম্পূর্ণ স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ করার শপথ নতুন করে নেওয়ার দিনও বটে।



