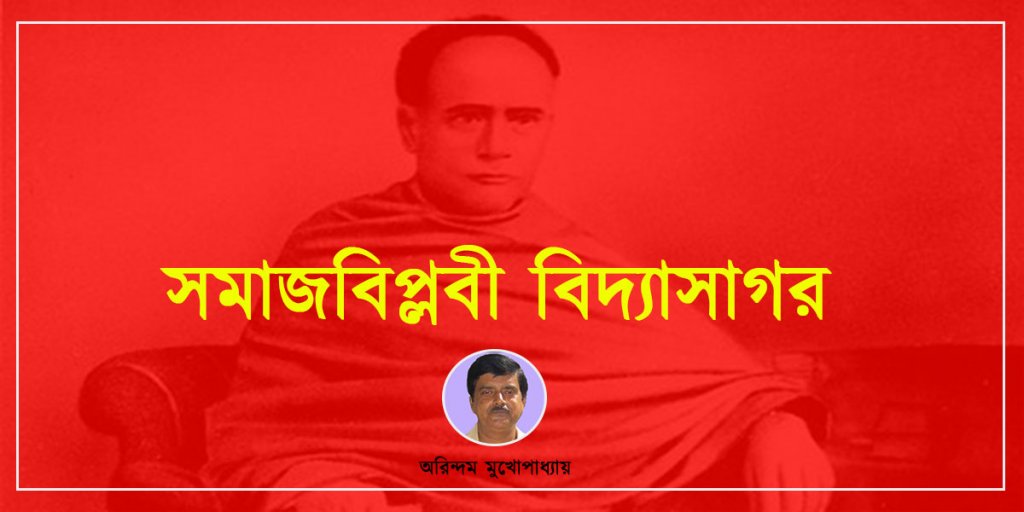
রাজা রামমোহন রায়ের পর বাঙালির সমাজজীবনে, মননে, চিন্তনে সব থেকে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী মনীষীর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ টোলো পন্ডিতের ঘরের ছেলে হয়ে এবং তৎকালীন সমাজবাস্তবতায় আপাদমস্তক সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তিনি উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ সমাজবিপ্লবীতে উন্নীত হয়েছিলেন। যা ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ঘটনা। ১৮২০ থেকে ১৮৯১—এই একাত্তর বছরের জীবদ্দশায় নিজের সর্বতোমুখী প্রতিভা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের জোরে তিনি শিক্ষা প্রসার ও সমাজ সংস্কারে বৈপ্লবিক ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম হয়েছিলেন। নারী শিক্ষার প্রসার, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান ও দর্শনে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষিত করার সাহসী প্রয়াস, বাংলা গদ্যসাহিত্যের গঠনশৈলীর উন্নয়নে প্রচেষ্টা, জাতিভেদ ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানসহ বাল্যবিবাহ-বিধবাবিবাহ-বহুবিবাহ রদে তাঁর অসাধারণ শাস্ত্র বিশ্লেষণ ও আইন প্রণয়নে সর্বস্ব পণ মৌলিক প্রচেষ্টাগুলি তৎকালীন সামাজিক অজ্ঞানতা, প্রতিকুলতা, অসহযোগিতার প্রেক্ষাপটে বিপ্লবী কর্মকান্ড রূপেই অভিহিত হবার যোগ্য। আজ এই মহান মনীষীর ২০৩ তম জন্মদিবসে তাঁর সম্পর্কে যৎসামান্য আলোচনার উদ্দেশ্যেই এই নিবন্ধের অবতারণা।
নিজের কৈশোর ও যৌবনে বিদ্যাসাগর কলকাতায় শিক্ষা ও কর্মজীবনের সূত্রে কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ‘ইয়ং বেঙ্গল’ আন্দোলনের রূপ। নির্বিচারে ভারতীয় ঐতিহ্যের সবকিছু অস্বীকার করে অদম্য ক্ষণস্থায়ী আবেগের বশে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা ও কৃষ্টির অন্ধ অনুকরণে মত্ত এই গোষ্ঠীর আন্দোলনের আবর্তে তিনি কোনোদিনই প্রবেশ করেন নি। তাঁর প্রখর সমাজবাস্তবতা ও বোধ থেকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এই ঝোড়ো আন্দোলন আবর্ত থেকে কোনোদিনই প্রবাহে পরিণত হতে পারবে না। অচিরেই ঝড় থেমে গিয়ে নিস্তরঙ্গ হয়ে পড়বে। তিনি ব্রাহ্ম সমাজেও নাম লেখান নি। ব্রাম্ভ সমাজের বেদের অভ্রান্ততা ও বেদান্ত দর্শনের সপক্ষে অবস্থানের তিনি ছিলেন বিরোধী। অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে একযোগে এই প্রসঙ্গে তিনি মতাদর্শগত বিতর্ক চালিয়েছেন ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকায়। সম্পূর্ণ আলাদা ধাতুতে গড়া মানুষ বিদ্যাসাগর ইয়ংবেঙ্গল এবং ব্রাহ্ম সমাজের দলে নাম না লিখিয়েও নিজস্ব স্বকীয় পথ অনুসরণ ক’রে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানবতাপ্রেমী, নিরীশ্বরবাদী ও যুক্তিবাদী সমাজ সংস্কারক হয়ে উঠেছিলেন। তাই বিদ্যাসাগরের চরিত্র ও কর্মের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে উত্তরকালের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, ”মাঝেমাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালি নির্মাণ করিতেছিলেন, সেখানে হঠাৎ দু’একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন?” বিদ্যাসাগরের জীবন আমাদের কাছে যেন এক কালোত্তীর্ণ কষ্টিপাথর—যার স্পর্শে আমাদের ত্রুটি, বিচ্যুতি, ক্ষতগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভাষায়, ” বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড়ো জিনিসকে ছোটো দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্র স্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড়ো বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ওই যন্ত্র একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন এবং এই যে বাঙালীত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি, তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। এই চতুর্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবল পর্বতের ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দন্ডায়মান থাকে, কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে ” বিদ্যাসাগরের জীবনের অন্যতম কীর্তি শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা। কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে থাকা দুর্বল হীনবীর্য একটি জাতিকে মনুষ্যত্ববোধ ও আত্মশক্তির উপর দাঁড় করাতে গেলে শিক্ষা ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই এই উপলব্ধি থেকেই তিনি শিক্ষাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ না করে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষা দপ্তরের সরকারি বিভিন্ন উচ্চপদে কর্মরত অবস্থায় শিক্ষা প্রসারের বিভিন্ন কাজে তিনি মৌলিকত্ব স্থাপন করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিতে যে সুর ধ্বনিত হয়েছে বিনয় ঘোষের ভাষ্যে—”সেই সুরটি হল পাশ্চাত্য বিদ্যার সঙ্গে ভারত বিদ্যার সমন্বয়য়”। তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে সমাসীন থাকার সময় বেনারস সংস্কৃত কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ ব্যালেন্টাইনের উপর কলকাতা সংস্কৃত কলেজের পরিদর্শনের ভার ন্যস্ত হয়। কলেজ পরিচালনা বিষয়ে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করলেও পাঠ্যসূচি বিষয়ে তিনি এমন কিছু সুপারিশ করেন যা নিয়ে প্রতিবাদ ব্যক্ত করতে হয় বিদ্যাসাগরকে। কারণ ব্যালেন্টাইনের সুপারিশে পাশ্চাত্য ভাববাদী দার্শনিক বার্কলের গ্রন্থ পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব ছিল। বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্য বিদ্যার সঙ্গে ভারত বিদ্যার সংমিশ্রণ চেয়েছিলেন কিন্তু কখনও ভাববাদকে গ্রহণ করেন নি। বস্তুবাদী দর্শনের সমর্থক হিসাবে তিনি ভাববাদী ও গোঁড়া হিন্দুত্ববাদী সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শন পড়ানোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে এই দুই দর্শন হল ভ্রান্ত দর্শন। একই কারণেই তিনি বার্কলের গ্রন্থ পড়ালে সুফলের চেয়ে কুফলই বেশি হবে বলে মনে করতেন। তাঁর মতে সংস্কৃত কলেজে হিন্দু ভাবাবেগ সহ বিভিন্ন বাধ্যতার কারণে সাংখ্য ও বেদান্তর মতো দর্শনগুলি পড়াতে হয়। কিন্তু এই ভ্রান্ত চিন্তার প্রতিষেধক হিসাবে ভালো ভালো ইংরাজি দর্শন শাস্ত্রের বই ছাত্রদের পড়ানোর দরকার। বার্কলের বই সেই প্রয়োজন মেটাতে পারবে না।
সংস্কৃত কলেজেবিদ্যাসাগর সংস্কৃতের পাশাপাশি ইংরাজি শিক্ষা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেন। দীর্ঘদিনের প্রথা ভেঙে ব্রাহ্মণ শুদ্র নির্বিশেষে সকল ছাত্রের জন্য কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। সংস্কৃত শিক্ষাকে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য তিনি বাংলা ভাষায় সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষার বই ‘ব্যাকরণ কৌমুদী’, ‘উপক্রমণিকা’ রচনা করেন। মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা না হলে গণশিক্ষা অসম্ভব। বিদ্যাসাগরের অঙ্গীকার ছিল “সেই হেতু আমার উদ্দেশ্য সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষার বিস্তার।” এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষ্যেই তিনি সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা বা আনুকূল্যের পরোয়া না করে নিজস্ব খরচেই বাংলার জেলায় জেলায় বাংলা মাধ্যম স্কুল প্রতিষ্ঠার কর্মযজ্ঞে মেতে ওঠেন। এর মধ্যে বেশিরভাগই ছিল বালিকা বিদ্যালয়। যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন একজন পুরুষ সাক্ষর হলে শিক্ষিত হয় একজন মানুষ, কিন্তু একজন নারী সাক্ষর হলে শিক্ষিত হয় গোটা পরিবার। তাই তিনি নারী শিক্ষার প্রসারে সবচাইতে বেশি উদ্যোগী হয়েছেন। ১৮৫৭-৫৮ সালের মধ্যে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর, নদীয়া জেলায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় তিনি স্থাপন করেছিলেন। আবার এই বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধের প্রতিক্রিয়ায় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে ইস্তফাও দেন।
বিদ্যাসাগর ছিলেন নিরীশ্বরবাদী। তাঁর কাছে মনুষ্য ধর্মই ছিল সবচেয়ে বড়ো ধর্ম। সমাজে নারীজাতির দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার অবসানকল্পে তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলন ও বহু বিবাহ রদে কঠোর কঠিন পরিশ্রম করেছিলেন। সতীদাহ নিবারণী আইন জারি হওয়ায় বাল্য বিধবাদের সুস্থ সামাজিক জীবনে পুনর্বাসনের ও সম্পত্তির অধিকারের প্রশ্ন জরুরি হয়ে ওঠে। এই প্রেক্ষাপটেই বিধবা বিবাহ প্রণয়নে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা মূর্ত হয়ে ওঠে। রক্ষণশীল সমাজে ভয়ংকর বিদ্রুপ ও আক্রমণের সামনে দাঁড়িয়ে অবিচল দৃঢ়তায় বিদ্যাসাগর শাস্ত্র বিশ্লেষণ, শাণিত যুক্তি ও মানবতাবাদের আদর্শ পাথেয় করে নিজের কর্মসাধনায় অবিচল থাকলেন। অবশেষে ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হল। বিদ্যাসাগরের ভাষায়, “বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম।—আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি—সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক, তাহা করিব। লোকের ভয়ে কদাচ সংকুচিত হইব না।” বিধবা বিবাহ ও বহু বিবাহ রদের প্রচেষ্টায় বিদ্যাসাগরের শাস্ত্র বিশ্লেষণ বস্তুতপক্ষে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের উপরে আঘাত। তাই ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের বিরুদ্ধাচরণ ছিল প্রত্যাশিত। বস্তুবাদী চেতনায় ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর উক্তি, “তাঁকে তো জানবার জো নাই। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত, যাতে জগতের মঙ্গল হয়।”।
জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এই মহাপুরুষ জীবনের শেষ পর্যায়ে নিজের পরিবার, আত্মীয়, কুটুম্ব এবং স্বগোত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছ থেকে অসম্মান অবমাননার শিকার হয়েও মানুষের ওপর বিশ্বাস হারান নি। আজীবন একাকীত্বের বোঝা বহন ক’রে এবং বহু আঘাতে দীর্ণ হয়েও তিনি তাঁর কর্মপথে অবিচল ছিলেন। রামকৃষ্ণের ধর্মীয় আহ্বান সত্ত্বেও তিনি দক্ষিণেশ্বরে না গিয়ে সাঁওতাল পরগনার কার্মাটারে সহজ সরল আদিবাসী সাঁওতালদের সঙ্গে দিন কাটিয়েছেন। যা তাঁর বস্তুবাদী সমাজবিপ্লবী সত্তার পরিচায়ক। বিশিষ্ট মার্কসবাদী ইতিহাসবিদ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, ” বিদ্যাসাগর যুগে মানুষ ও সমকাল প্রস্তুত ছিল না বৈপ্লবিক উদ্যোগের জন্য। এটাই হল বিদ্যাসাগর-জীবনের (এবং অন্যান্য বহু ভারতীয় মহামতির জীবনের) ‘ট্রাজেডি’।” বর্তমান প্রজন্মের সবাইকে বিদ্যাসাগর আন্দোলনের আরব্ধ বার্তাকে বহন করার গুরু দায়িত্ব পালন ও দায়বদ্ধতা প্রমাণ করার মধ্য দিয়েই সেই ‘ট্রাজেডি’র পাপ স্খালন করতে হবে।



